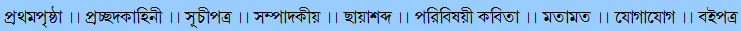
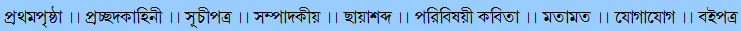
উদাসীনতার সাহিত্য
কমল
চক্রবর্তী
তাঁর প্রথম
উপন্যাসের
প্রথম
পংক্তিতে
লিখেছিলেন
উদাসীনতা
মানুষের
নিজস্ব
ব্যাপার।
উদাসীনতার
সাহিত্য সেই
নিজস্ব
উদ্বেগ ও আত্মাভিমানের
মাধ্যমেই
রচিত হয় যা
অন্যের কাছে
কখনো অলসতা,
কখনো
অনুর্বরতা বলে
মনে হতে পারে।
তবে উষ্মার নেপথ্যে
যেমন দিন দিন
ধ’রে আধপোড়া
অনুভূতির
জ্বালানি জড়ো
হয়েছিলো,
উদাসীনতার
ভিতেও নিশ্চয়ই
থাকতে পারে মনের
অনেক সূক্ষ্ম
ফাটল যা ধরা
পড়বে একমাত্র
আতসকাঁচের
নিচেই।
এসব কথা উঠছে
কৌরব অনলাইনের
আচমকা
গতিরোধের
প্রসঙ্গে। গত
বছর কৌরব
অনলাইনের ২০
বছর পূর্ণ হলো
৫৪ নম্বর
সংখ্যায়। গড়ে
৩টে সংখ্যা
হয়েছে এই বিশ
বছর ধরে। ৬০
নম্বর সংখ্যা
হবার কথা ছিলো
৫৪র বদলে।
১৯৯৮-২০০০
তখনো
আন্তর্জালে
হামা দিচ্ছে
বাংলা ভাষার
প্রযুক্তি,
ফলে ১টার বেশি
সংখ্যা বের
করা যায়নি।
কিন্তু যতি
পড়লো ২০ বছর
পেরিয়ে – এক দীর্ঘ
বিলম্ব, যাকে
এক এক সময়ে
অনিঃশেষ মনে
হচ্ছিলো। শেষ
পর্যন্ত অনেক
বাধা বিপত্তি
পেরিয়ে ৫৫
নম্বর সংখ্যা
যে বেরলো তার
প্রায় গোটাটাই
সব্যসাচী
সান্যালের
প্রয়াসে। এই
দীর্ঘ বিরতি
পর্বে যে
কবি-পাঠকরা
খোঁজাখুঁজি
করেছেন
কৌরবের, তাদের
সবাইকে অজস্র
ধন্যবাদ
জানিয়ে এই প্রতিশ্রুতি
যোগ হলো, যে
কৌরব অনলাইন আবার
তার আগের
গতিতে
প্রকাশিত
হবে।
সব্যসাচী,
শুভ্র ও সোমনাথ
আড়মোড়া
কাটিয়ে উঠছেন,
তরুণতররা
মকশো করছেন
পাশাপাশি, এবং
অগ্রজদের
লেখালিখি
নিয়েও আমরা
ভাবছি –
কীভাবে তাঁদের
কাজকর্মের একটা
নিজস্ব
বারান্দা তৈরি
করা যায় এ
বাড়িতে।
আরো একবার
কৌরব
অনলাইনের প্রণাম
বারীন
ঘোষালকে, তাঁর
প্রথম
মৃত্যুবার্ষিকিতে।
গত সংখ্যার
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
পুনঃপ্রকাশ
করার আবেদন
জানিয়েছেন
কেউ কেউ। সে
আদেশ রাখা হলো
যেমন, তার
সাথে এ প্রশ্নও
তুললাম –
আন্তর্জাল
মাধ্যমে আবার
পুনঃপ্রকাশের
মানে কী? কেন
পুনঃপ্রকাশ
করতে হবে?
পাঠক কি অলস
হয়ে পড়ছেন?
====
কল্পপরিচিতির
কবিতা
আর্যনীল
মুখোপাধ্যায়
‘কল্পপরিচিতির
কবিতা’ – এক নতুন
শব্দবন্ধ। এই নির্মাণের
প্রয়োজন পড়লো সেই
কবিতার কথা বোঝাতে
যেখানে কবি এক
কল্পিত মানবের
পরিচিতি গ্রহণ
ক’রে তার মনন, ব্যক্তিত্ব,
স্থান, জগতে প্রবেশ
ক’রে, সেই নতুন ভূমিকা
বা অবতারে লেখেন।
জন
অ্যাশবেরির অনুবাদে
আর্তুর র্যাঁবোর
জীবনের শেষ বই
‘Illuminations’ বা ‘উদ্দীপন’। বইয়ের
ভূমিকায় এক জায়গায়
অ্যাশবেরি লিখেছেন
–
‘Yet more essentially absolute modernity was for him
(Rimbaud) the acknowledgement of the simultaneity of all of life, the condition
that nourishes poetry at every second. The self is obsolete: In Rimbaud’s
famous formulation, “I” is “someone else” (“Je est une autre”). In the
twentieth century, the co-existing, conflicting views of objects that the
Cubist painters cultivated, the equalizing deployment of all notes of scale in
serial music, and the unhierarchical progression of bodies in motion in the
ballets of Merce Cunningham are three examples of many of this fertile
destabilization.”
সুতরাং
আমার পূর্ববিশ্বাস
অনুযায়ী কোনো কিছুই
আসলে যেমন ‘নতুন’
নয়, আগে ছিলো বা
আছে; তারই এক নবপ্রযোজনা
ঘটছে এই ‘কল্পচরিতের
কবিতায়’। এবং র্যাঁবোর
লেখাতেই এই বিশ্বাস
প্রোথিত ছিলো।
বহু কবি, নানা দেশে,
কল্পচরিতের ব্যবহার
করেছেন কবিতায়।
আমরা কয়েকটা জানি।
যেমন ফের্নান্দো
পেসোয়া। কিন্তু
পেসোয়ার যে heteronymy, তার কতোটা
নিজেকে আড়াল করতে
আর কতোটা অন্যের
চেতনায়, চরিত্রে,
দেশকালে নিজেকে
নিক্ষেপ ও রূপান্তরিত
করতে সে বিষয়ে
সন্দেহ থেকে যায়।
পরিবিষয়ী
কবিতার সহলিপি
ভাবনা নিয়ে অনবরত
নিয়োজিত থাকতে
থাকতেই হয়তো পরিবিষয়ী
কবিতা দলের অন্তত
তিনজনের লেখার
মধ্যে ধরা পড়েছে
এই কল্পপরিচিতির
উপস্থিতি। মজার
ব্যাপার, এদের
কেউই একে অন্যের
দ্বারা এ বিষয়ে
প্রভাবিত হননি,
এ নিয়ে আলোচনাও
করেননি এবং এঁদের
কল্পিত চরিত্রগুলো
বিদেশী এবং একেকজনের
ক্ষেত্রে এক একটা
দেশ, কাল ও সমাজের।
সবচেয়ে আগে
এটা আসে শুভ্র
বন্দ্যোপাধ্যায়ের
‘জোয়াকিম মন্ডলের
কবিতা’য় (বৌদ্ধ
লেখমালা ও অন্যান্য
শ্রমণ, কৌরব, ২০১২)। জোয়াকিম
(বা হোয়াকিম) মন্ডল
এক চিত্রশিল্পী
যে ইউরোপে গোপন
জীবন কাটাচ্ছে
এক বেআইনি অনুপ্রবেশকারী
হিসেবে। কোনো দেশের
খাতায় তার নাম
নেই। রাষ্ট্রের
কাছে যার পরিচিতি
গুপ্ত, সেই মানুষেরই
ছবির ক্যানভাসে
ধরা পড়ে তার গোটা
মনন-পরিচিতি। তারই
কলমে শুভ্র লেখে,
নিজের নয়, জোয়াকিম
মন্ডলের কবিতা।
মুখবন্ধে সে স্পষ্ট
জানিয়ে দেয় –
‘HC LÏha¡¬®m¡ q®a f¡la Ýk ÝL¡eJ ÝhBCÏe
Ae¤fË®hnL¡l£lz CJ®l¡®fz Ýcn ÝR®sÏR®m¡ 15 Ïc®el Ïip¡uz hRl ÝfÏl®u ÝN®Rz Eiu
Ýc®nl plL¡Ïl M¡a¡u Ýp Ïe®M¡ySz kÏc Hi¡®h a¡l Ïe®Sl ÝO®V¡u, Be¤ù¡ÏeLi¡®h
Ïe®M¡yS, L¡ÏV®u Ïc®a f¡®l BlJ L®uLV¡ hRl,a¡®L jªa h®m ÝO¡oZ¡ Ll¡ q®hz ÝS¡u¡ÏLj j™m HL fË¡š²e RÏh ByÏL®uz
haÑj¡®e c¡m¡®ml q¡a d®l CJ®l¡®f e¡e¡lL®jl ÝR¡V L¡®S hÉÙ¹z f¡®L Q®œ² Bj¡l p®Â
a¡l fÏlQu quz a¡l LÏha¡l Lb¡ S¡e®a f¡Ïlz HC LÏha¡¬®m¡ ÝpM¡®e Ýb®LC ÝeJu¡z’
কবিতার
একটা ছোট নমুনা
রাখলাম –
2
Ýl¡j¡Ïeu¡l ÝSÏeL¡ h¡ a¡l ja
Ýk®L¡eJ f§hÑ CJ®l¡®fl ÝcqS£Ïhe£®L
BÏj Ýcn ÏS®‘p LÏlÏe öd¤
Lb¡h¡aÑ¡ c£OÑ q®m ÝVl f¡C a£rÁ
radje£z
ÝL¡eJ l¡Ù¹¡l lw ,L¡NS, L¡fs, ÝW¡yV
m¡m q®m Lø qu Ýa¡l
f¡®LÑl ejË A®ƒ¡hl ÝW®m f¡ul¡l
T¡yL Q®m ÝN®m ÝcÏM
q¡Ju¡u L¡m®Q ÝR¡f, AiÉÙ¹ l¡aS¡N¡
ÝQ¡®Ml ÝL¡®m
Bj¡®cl
ec£j¡aªL EfL§m!
hC®ul S£he¬®m¡
j§ÏaÑ q®u HMe ÏØV®ml hªÏø®a Ýi®S
Ýf®uÏR ÝN¡fe
X¡uÏl®az
eNÀa¡l
Ïpmɤ®uV Ïi®S EW®m Øf®nÑ Øf¾cj¡e HLV¡ X¡e¡
R¡C J Ýe¡ea¡
h¡a¡p
Ol R¡s®mC
Na¡e¤NÏaL h¤ch¤®c Ýj¡s¡ Ýc¡L¡e, i¡p®R
e£®Q N®aÑ œ²j¡Na k¡a¡u¡a, O®l ÏgÏl
f¡n Ïg®l b¡L¡ Es¡e R¤y®u®R ÏOÏ”
Ù¹e
S¡em¡ Ïc®u ÝY¡L¡ Ýp„ n®fl Ïeu®e
Øfø HLV¡ R¤Ïl Ïc®u ßaÏl f¡ÏM
ÝhXp¡CX ÝVÏh®m
ফের্নান্দো
পেসোয়ার কবিতার
‘বহুনামবাদ’ (heteronymy) ও ফিউচারিস্ট
ম্যানিফেস্টোর
(১৯০৯) কয়েকটা প্রস্তাবনা
অনুযায়ী কল্পপরিচিতি
ইউরোপীয় কবিতা
গত শতকের গোড়াতেই
পরিচিত হয়ে উঠেছিলো। পেসোয়া ও
আন্তোনিয় মাচাদো
(ওঁর কল্পপরিচিতের
রচনা ‘খুয়ান দে
মাইরেনা’)র একটা
সূক্ষ্ম প্রভাব
ইস্পানি কাব্যসাহিত্যে
নিমজ্জিত শুভ্রর
কবিতায় পা রেখেছে।
একেবারে
সমানুপাতিকভাবেই
২০১৭ সালের বইমেলায়
আসে বাংলাদেশ থেকে
প্রকাশিত সব্যসাচী
সান্যালের বই
‘তদোগেন গিরতের
কবিতা’। তারও
আগে, ‘প্রিয় পিয়ক্কড়’
কাব্যগ্রন্থে
সব্যসাচী লিখেছিলো
–
‘আমি বিশ্বাস
করি, শিল্প কেবল
অভ্যাসের বাইরেই
গড়ে ওঠে—প্রাকৃতিক
উপাদান নিয়েও সে
প্রকৃতির থেকে
বিচ্যুত হয়ে বেড়ে
ওঠে—ফলে আমি নিজেকে
লিখি না, নিজের
স্বভাব থেকে দূরে
এক অপরিচিতের কথা
লিখি…উদ্ধৃতিচিহ্নের
থেকে ছাড়িয়ে আনি
বস্তুর চিৎকারটুকু—তাকে
লিখি…'
‘তদোগেন গিরতের
কবিতা’-কে কবি অনুবাদ
কবিতা বলতে চান।
কে এই তদোগেন গিরতে? সব্যসাচীর
বক্তব্য অনুযায়ী
‘তদোগেন মঙ্গোলিয়ার
ওন্দোরহান বিশ্ববিদ্যালয়ে
কম্পারেটিভ লিটারেচার
পড়ান। কবিখ্যাতি
সেভাবে নেই। কোনো
প্রকাশিত বই নেই।
সময় কাটানোর জন্যই
লেখালিখি করেন।
তার নিজের কথায়; “কবিতা নিয়ে সেরকম
কোনো অ্যাম্বিশন
নেই। তা ছাড়া আমার
লেখাগুলি যে আদৌ
কবিতা—মঙ্গোলিয়ার
কোনো দৈনিক বা
পত্রিকা সে কথা
স্বীকার করে না।”’ কল্পপরিচিতির
এক তুমুল উদাহরণ
এই বই। আদতে এই
কবিতা সব্যসাচী
সান্যালেরই, অথচ কোনোভাবে
তার কবিতার অগ্রপশ্চাতের
সাথে মেলেনা এই
লেখা। যে মঙ্গোলিয়ায়
কবি কোনোদিন যাননি,
সেই মঙ্গোলিয়ার
গাছপালা, পশুপাখি,
শহর-গ্রাম,
ভাষা, সংস্কৃতি,
বিজ্ঞান সম্বন্ধে
যথেষ্ট পড়াশোনা
ক’রে, আনুমানিক
সে বিদেশে নিজেকে
সম্পূর্ণ নিমগ্ন
ক’রে লেখা এই কবিতা
ভিনদেশের কল্পমানব
তদোগেন গিরতের
কবিতাই হয়ে উঠেছে।
একটা প্রখর dystopia কাজ
করে তদোগেনের কবিতায়, একটা
মালিন্য, নোংরা,
মলমূত্রবীর্যে
ছাওয়া scatalogical জীবন
ও কড়া পড়া মননের
কবিতায় তদোগেন লেখেন –
আমি নোংরা
মেয়েদের কাছে যাব
কাঠের
নথ নিয়ে যাব
আমার বাহুর
মাংসে গিঁথে গোবি
ভাল্লুকের দাঁত
আমার কোনো
নিষেধ নেই
আমি নোংরা
মেয়েদের মুখের
ভেতর
ঘুরে দাঁড়াচ্ছি, আর কাঁপছি
কোঁচকানো
মুখের চামড়া টান
করে দিচ্ছি
আমার কোনো
নিষেধ নেই
ঘাসের
মধ্যে উঠে দাঁড়াচ্ছে
সারস
ওর চোখের
পাতা লাল
ওর পিঠের
রঙ কালো
চকচকে
দুই দাবনার মাঝে
সবচে মিষ্টি ওর
পুটকি
তদোগেন তার
নিজের পরিচিতি
নিয়ে পাঠকের সাথে
খেলা করে এমনভাবে
যেন সে মত্ত, তাকে
তখন বিশ্বাসও করা
যায় না, তার কোনো
কথা, কবিতা সিরিয়াসলি
নেওয়া যায় না, এবং
সেটা এতটাই সত্যি
হয়ে ওঠে যে এই কবিতা
যখন পত্রপত্রিকায়
বেরচ্ছে, আমি পড়তেও
চাইনি। কয়েকটা
পড়ে মুখ ফিরিয়ে
নিই এবং সব্যসাচীর
কাছে আমার বিরক্তি
প্রকাশ করি। প্রয়াত
ইন্দোনেশীয় কবি
চৈরিল আনোয়ারের
কন্ঠ যেন তদোগেন
শুনতে পাই, টের
পাই তার জীবনযাপন
চৈরিলেরই সমান্তরাল।
সব্যসাচী তখন জানায়
সে চৈরিলের কবিতা
পড়েনি কখনো। তদোগেন আমাদের
মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে
বলেন –
আমার নাম
তদোগেন গিরতে
তদোগেন
গিরতে বলে কেউ
নেই
আমার বউ
দুশ্চরিত্তির
আমার বউয়ের
বোঁটা খুঁড়ে দিয়ে
যায় কাক
আমি স্তেপ
পেরিয়ে আর নদী
পেরিয়ে
নোংরা
মেয়েছেলের কাছে
যাই
আর দেখি
ওর বিছানায় রাত্রি
আর দেখি
ওর বিছানায় দু’পায়
রাত্রিকে জড়িয়ে
বনশুয়োর
আমার বউ
দুশ্চরিত্তির
আমার বউ
বলে কিছু নেই
আমি নোংরা
মেয়েছেলের কাছে
যাই
পুরো মঙ্গোলিয়ায়
কোনো নোংরা মেয়েছেলে
নেই।
২০১৭র
বইমেলায় কলকাতা
গিয়ে বইটা হাতে
পাই। জানতে পারি
তদোগেন এক কল্পচরিত্তির।
চমকে উঠি। চমকে
ওঠার একটা দ্বিতীয়
কারণও ছিলো। সেটা
আমার নির্মিয়মান
কবিতাপ্রকল্প
‘একক ইশ্তাহার’-য়ের জন্য। ২০১২
সাল থেকে লেখা
হচ্ছে এই প্রকল্পের
কবিতা। নিক্ষেপ
ও রূপান্তকরণের
দিক থেকে ভাবলে
আমার নিজের ক্ষেত্রে
পরিচিতির চেয়ে
পরিচিতিহীনতাই
ছিলো প্রধান। যে
লোক নাম নিলো ‘অনাম
আন্দ্রেস’ (from Anam or Anom – Anonymous) তার
মূল পরিচিতি কেউ
জানলো না, সে নিজেও
নয়। তার আয়না কাউকেই
দেখায় না, গড়ে উঠলো
এক সম্পূর্ণ নতুন
পরিচিতি, নতুন
দেশে।
কবিতার
পশ্চাতে একটা কাহিনি
বলা আছে। সেই কাহিনির
নায়কই লিখছে তার
নিজের কথা, তার নিজের কবিতা।
নায়ক এক যুবক।
বাংলা জানে। আর
কিছু সে জানে না।
এমনকি নিজের নামও
নয়। বংশপরিচয়,
দেশ, বয়স
কিচ্ছু না। এক
জাহাজডুবিতে তার
পূর্বস্মৃতি লোপ
পায়, কিন্তু
জ্ঞানস্মৃতি রয়ে
যায়। লাতিন আমেরিকার
কলোম্বিয়ার একটা
দ্বীপ সান আন্দ্রেস।
সেখানে সে জাহাডুবি
থেকে ভেসে উঠে
উদ্ধার পায়। যেমন
‘উদ্ধার’ পায় ‘উদ্ধৃতি’।
ফলে
তার সমস্ত কবিতা
শুরু হয় এক উদ্ধৃতি
দিয়ে, সেই উদ্ধৃতির
প্রত্যুত্তরে
সে লেখে। নতুন
নাম নেয় সে যুবক
– অনাম আন্দ্রেস।
তার কবিতাই ‘একক
ইশ্তাহার’। অনাম
লেখে –
‘প্যারালিসিস
শূন্যের মধ্যে
একটা গর্ত খোদাই
করে। তাকেই বলে
লেখা…’
-
বুস্কে
┌ ┐
যতোটা মুগ্ধতায়
আমরা সুস্থির হয়ে
খাকতে পারি তার
সবটাই
নড়চড়ে
সেই বিরতিতে
যে চিন্তার চিনি
পিপীলিকাবাহিনী
নিয়ে আসছে
সেসব মিলিয়েও
কিয়দংশ।
শূন্যতা একেবারে
নিরবয়ব না, কিয়দংশ
তার মধ্যেও
একটা গর্ত খোদাই
হয়
গাছের গা দেখবেন
- বোঝা যায়কি
গত বসন্তের কথা?
দু-তিনদিন
টানা সেই নবাগত
কাঠঠোকরার যৌবননাশ?
না?
দৃশ্যের ধুতি
ছিঁড়তে হবে। ‘বা!’ বলা স্থগিত
রাখতে হবে
মনোনিবেশ
করতে হবে
তখন জানা
যায় স্থবিরতাই
সমস্তের শুরু।
এমনকি মনোযোগের
প্রয়াস
যা এক সাকার
পিগি-ব্যাঙ্ক
মৌচাক
└ ┘
এইভাবেই
সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন
থেকেও কী অদ্ভুতভাবে
তিন পরিবিষয়ী কবি
নিজেদের মতো, ভিন্ন
সময়ে কল্পপরিচিতি
নিয়ে কাজ করতে
থাকে। তাদের কল্পচরিতও
আসে আলাদা আলাদা
ভূপ্রান্ত থেকে।
জোয়াকিম মন্ডল
নাগরিকত্ব লুকিয়ে
রয়েছে ইউরোপে
–স্পেনে; তগোদেন
গিরতে এশিয়ায়,
মঙ্গোলিয়ার আইনি
বাসীন্দা; আর আত্মপরিচিতি
সম্পূর্ণ হারিয়ে
নতুন নাম নেওয়া
অনাম আন্দ্রেস,
ইস্পানি শেখে আর
শেফ্ হিসেবে কাজ
করে লাতিন আমেরিকার
এক দ্বীপে। তিন
মহাদেশ থেকে আসে
বাংলা কবিতার তিন
কল্পপরিচিতি।
এই বিচিত্র সমানুপাতিক
প্রবণতা পরিবিষয়ী
কবিতার এক নবপর্যায়।
===
আমি একবিন্দু
একবিন্দু মধু নিয়েছি
তোদের কিছু
গন্ধ কিছু গন্ধ
ধার নিয়েছি
১।
বিষ্ণু দে, ‘স্মৃতি
সত্তা ভবিষ্যত’,
দেজ, ১৯৬৬।
২।
Image Music Text, Roland Barthes. Tr. By Stephen
Heath, Hill & Wang,
New York,
1977.
৩। Notes on Conceptualism, Robert Fitterman and
Vanessa Place, Ugly Duckling
Presse, 2009.
৪।
পরিবিষয়ী কবিতা
আন্দোলন সংখ্যা, কৌরব ১১১, কলকাতা বইমেলা
২০১১।
৫।
শুভ্র
বন্দ্যোপাধ্যায়,
বৌদ্ধ লেখমালা
ও অন্যান্য শ্রমণ,
কৌরব, ২০১২।
৬।
সব্যসাচী
সান্যাল, তগোদেন
গিরতের কবিতা,
বেহুলা বাংলা,
বাংলাদেশ, একুশে
বইমেলা ২০১৭।
৭।
অনাম আন্দ্রেসের
একক ইশ্তাহার,
আর্যনীল মুখোপাধ্যায়,
নির্মিয়মান কাব্যগ্রন্থ।
Copyright ©
2018 Aryanil Mukhopadhyay Published 31st Dec, 2018.